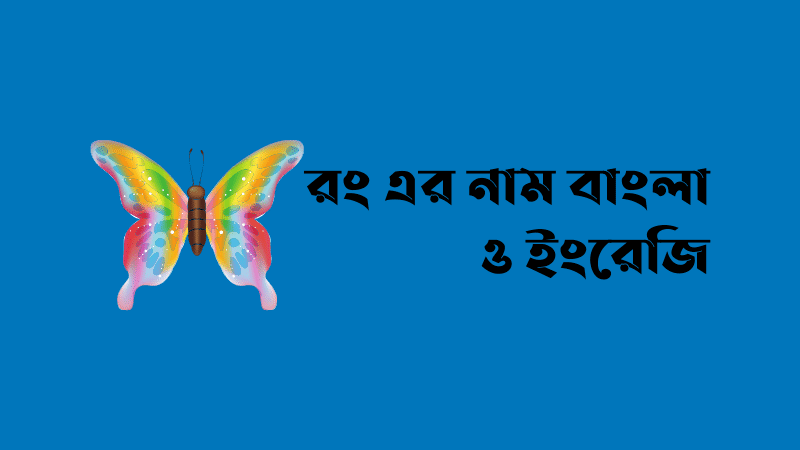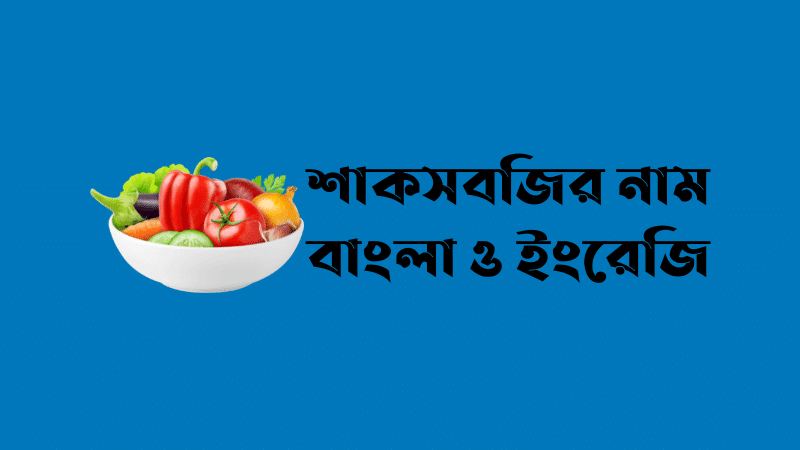নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বৃত্তান্ত ও জীবনচক্র
জীববিদ্যার জ্ঞান বলতে যে শুধু নানা জীব প্রজাতি সম্পর্কে জ্ঞানের সমাহার বোঝায় তা নয়। বিভিন্ন প্রজাতি তাদের জীবনযাত্রার জন্য পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ আর একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই এই পরস্পর-সম্পর্কের বিষয় না জানলে জীববিদ্যার জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। এদিক থেকেও ক্রান্তীয় অঞ্চলের জীবসমাবেশ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান আজও অতিমাত্রায় সীমিত।
ইউনেস্কোর হিসেব অনুযায়ী ক্রান্তীয় অঞ্চলে যত বিজ্ঞানী গবেষণায় নিয়োজিত তার চেয়ে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গবেষণারত বিজ্ঞানীর সংখ্যা অন্তত ত্রিশ গুণ বেশি। পৃথিবীতে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লাখ প্রজাতির জীবের বাস; এর মধ্যে প্রায় ত্রিশ লাখ প্রজাতি বাস করে গ্রীষ্মমণ্ডলে। অথচ বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত মাত্র পাঁচ লাখ প্রজাতির জীবের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করতে পেরেছেন। অর্থাৎ স্পষ্টতই গ্রীষ্মমণ্ডলের জীবদের বিবরণ এবং তাদের পরস্পর–সম্পর্কের বিষয়ে জ্ঞান জীববিদ্যার স্বার্থে শুধু নয়, মানবসভ্যতার বিকাশের জন্যই আজ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।
নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সব দেশের বাসিন্দারা যে কেন ‘মাঝারি আয়ের’ বা ‘ধনী’ (মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন এক হাজার ডলারের বেশি) আর ক্রান্তীয় অঞ্চলের সব দেশের বাসিন্দারা কেন ‘দরিদ্র’ বা ‘অতি দরিদ্র’ তার নানা কারণ রয়েছে। সব কারণ যে খুব স্পষ্ট এমনও বলা যায় না। তবে সাধারণভাবে নাতিশীতোষ্ণ দেশগুলোর চেয়ে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশগুলোর উৎপাদনশীলতা অনেক কম। পৃথিবীর প্রায় সবগুলো সচ্ছল দেশই নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে; আবার প্রায় সব দরিদ্র দেশই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে। এই দু’অঞ্চলের জলবায়ু, মাটি আর জৈব পরিবেশের পার্থক্য হয়তো কিছুটা পরিমাণে এই বৈষম্যের জন্য দায়ী।
উদ্ভিদ একমাত্র কারবন ছাড়া তার দেহের আর সব প্রয়োজনীয় উপাদান প্রধানত মাটি থেকে সংগ্রহ করে। এসব প্রয়োজনীয় উপাদানের মধ্যে কেবল পানি, নাইট্রোজেন, গন্ধক আর ক্লোরিন জলবায়ুর চক্রের মাধ্যমে আবর্তিত হয়। অন্যান্য পুষ্টিবস্তু যেমন ফসফরাস, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং অন্যান্য অনেক ‘গৌণ’, মৌল শেকড়ের কাছাকাছি পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকলেই কেবল উদ্ভিদ তাদের গ্রহণ করতে পারে। এদিক থেকে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মাটি আর নিরক্ষীয় বনাঞ্চলের মাটিতে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। শেষোক্ত মাটি প্রবল বর্ষণের ফলে প্রায় সম্পূর্ণভাবে পুষ্টিরিক্ত। এজন্য নিরক্ষীয় বনাঞ্চলের উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের কথা না জানলে এই অঞ্চলের কৃষিতে সাফল্য অর্জন হবে দুরূহ।
প্রায় সব উষ্ণমণ্ডলীয় বনাঞ্চলে জমির অনুর্বরতার একটি চিরাচরিত সমাধান হল ‘জুম’ চাষ। এই ব্যবস্থায় বনের অল্প কিছু এলাকায় গাছপালা কেটে ফেলে আগুন লাগিয়ে পোড়ানো হয়। এর ফলে দ্রবণীয় ছাই-এর আকারে উদ্ভিদদেহের সারবস্তু মাটিতে মেশে। এই মাটিতে বীজ ফেললে প্রথম বছর ফসল ভালই পাওয়া যায়।
কিন্তু সার নিঃশেষ হয়ে এলে বা বৃষ্টিতে ধুয়ে গেলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বছরে আর তেমন ভাল ফসল হয় না। তখন অন্য আরেক এলাকায় আবার এমনি বন পুড়িয়ে ছাই করে সেখানে ফসল বোনা হয়।
আমাজান নদীর অববাহিকায় দেখা গিয়েছে জুম চাষের এলাকা যদি হয় এক হেক্টরের কম আর একই জায়গায় দুবার চাষের মধ্যবর্তী সময় হয় এক যুগ বা তার বেশি তাহলে এই পদ্ধতির চাষে নিরক্ষীয় বনাঞ্চলের পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। অবশ্য এ পদ্ধতিতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারের দু’জনের বেশি লোকের খাদ্য-সংস্থান সম্ভব নয়। গ্রীষ্মমণ্ডলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ক্রমেই জুম চাষের এলাকা বাড়ছে; পর্যায়ের সময় কমছে। আর তার ফলে নিরক্ষীয় বনাঞ্চলের অস্তিত্ব হয়ে পড়ছে বিপন্ন। অথচ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের কৃষিপদ্ধতি সরাসরি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চলে প্রয়োগ করার চেষ্টা তেমন সফল হয়নি। গ্রীষ্মমণ্ডলে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য এসব অঞ্চলে জমির প্রকৃতি, জমিতে অণুজীবের উপস্থিতি ও তাদের জীবনচক্র ইত্যাদি সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন।
গ্রীষ্মমণ্ডলে কৃষির অন্যান্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে কীটপতঙ্গের ক্ষতিকর প্রভাব এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর নানা ধরনের ব্যাধি। এসব সমস্যা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেও আছে; কিন্তু সেখানে শীতকালে তাপমাত্রা এমন নিচে নেমে যায় যে, তাতে কীটপতঙ্গ আপনা আপনি যথেষ্ট পরিমাণে দমন হয়। শীতের পর অবশ্য কীটপতঙ্গের সংখ্যা বেড়ে ওঠে; কিন্তু যে পরিমাণে বাড়ে তা নিয়ন্ত্রণের উপযোগী নানা প্রযুক্তি ইতিমধ্যে উদ্ভাবিত হয়েছে। পরবর্তী শীত ঋতুতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আবার কীটপতঙ্গের সংখ্যা কমে আসে। কোন কোন মরুসদৃশ এলাকায় প্রবল খরার প্রকোপ ছাড়া এ ধরনের আবহাওয়াগত কীট নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রীষ্মমণ্ডলে নেই।
অবশ্য গ্রীষ্মমণ্ডলে অন্য ধরনের প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে; যেমন বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ প্রজাতির স্থানিক বিচ্ছিন্নতা এবং নানা ধরনের কীটপতঙ্গভুক পাখি, পোকামাকড় প্রভৃতির অস্তিত্ব। এই পরিবেশে আধুনিক কৃষিব্যবস্থা প্রয়োগ করে একই ফসল যখন ঘনসংবদ্ধ আকারে চাষ করা হয় তখন তা এ অঞ্চলের সনাতন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এমনকি কীটনাশক ওষুধের ব্যবহারও খুব কার্যকর হয় না, কেননা এসব ওষুধের বেশির ভাগ প্রচণ্ড বৃষ্টিতে উদ্ভিদের গা থেকে ধুয়ে নেমে যায়। বরং কীটনাশক নানা রাসায়নিক বস্তুর অতিপ্রয়োগের ফলে প্রতিরোধক্ষম প্রজাতির কীটপতঙ্গের উদ্ভব ঘটে। সেই সাথে কীটপতঙ্গভুক প্রাণীদের দেহে বিষাক্ত রাসায়নিক বস্তু সঞ্চিত হয়ে তাদের বংশ লোপ পেতে থাকে। তার ফলে ক্রমেই আরো তীব্র, আরো বেশি কীটনাশক ওষুধের প্রয়োজন দেখা দেয়। ইতিমধ্যে মধ্য আমেরিকার কোন কোন দেশে কীটনাশক কেনার ব্যয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তুলা চাষের মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ এবং তার ফলে চাষীরা তুলা চাষ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে।
নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতির সংখ্যা কম, কাজেই তাদের মধ্যে পরস্পর নির্ভরতার সম্পর্কও অপেক্ষাকৃত সরল। সে তুলনায় গ্রীষ্মমণ্ডলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতির সংখ্যা অনেক বেশি; আর তাদের মধ্যে পরস্পর নির্ভরতার সম্পর্কও অপেক্ষাকৃত জটিল। এ অঞ্চলে বছরের বিভিন্ন সময়ে আবহাওয়ার আর্দ্রতার যে তারতম্য ঘটে সে হিসেবে আলোক বিন্যাস বা উষ্ণতার তেমন তারতম্য ঘটে না। এই পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের শারীরবৃত্তিক বা আচরণগত প্রকৃতি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল থেকে ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।
আগাছা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও নাতিশীতোষ্ণ আর ক্রান্তীয় অঞ্চলের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ ঘটে। ক্রান্তীয় অঞ্চলে জমির স্বল্প সারবস্তুর ভাগ নিতে ফসলের সাথে প্রতিযোগিতায় নামে নানা ধরনের আগাছা। সচরাচর খাদ্যশস্যের তুলনায় এরা খরা, উষ্ণতার তারতম্য, প্রচণ্ড সূর্যকিরণ বা অতিবর্ষণ সইতে পারে ভাল; নানা বিচিত্র প্রজাতির হবার দরুন এদের নিজেদের মধ্যে পুষ্টি গ্রহণের প্রতিযোগিতাও কম। এসব আগাছা দমনের ব্যয় মোট কৃষি উৎপাদনের ব্যয়ের সাথে যোগ হয়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের আগাছা দমন পদ্ধতি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে হুবহু প্রয়োগ করার চেষ্টা সফল প্রমাণিত হয়নি।
গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সবই যে উচ্চ ফলনের প্রতিকূল এমন মনে করা ভুল হবে। উদ্ভিদের অস্তিত্ব আর পরিপুষ্টির একটি প্রধান উপাদান হল সূর্যকিরণ। সূর্যকিরণ পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে যেমন সুলভ্য এমন আর কোথাও নয়। উদ্ভিদে শারীরবৃত্তিক বিপাকের
উপযোগী উষ্ণতাও গ্রীষ্মমণ্ডলেই সবচাইতে অনুকূল। দেখা গিয়েছে ভূমির উর্বরতা আর পানি সরবরাহের ঘাটতি না পড়লে অনুরূপ পরিবেশে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের তুলনায় গ্রীষ্মমণ্ডলে উদ্ভিদের উৎপাদনশীলতা প্রায় দ্বিগুণ। অর্থাৎ গ্রীষ্মমণ্ডলে কৃষি উৎপাদন, বনায়ন এবং পশুপালনের প্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলো নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারলে জীববিদ্যার প্রয়োগ এসব সমস্যার সমাধানে অনেকখানি সহায়তা দিতে পারে।
অবশ্য উষ্ণমণ্ডলের উৎপাদনশীলতার মূল সমস্যা সম্পর্কে বিজ্ঞানের নানা বিভাগের কর্মীরা সবাই একমত নন। কারো মতে আবহাওয়া, জমি, কীটপতঙ্গ এসবই হল প্রধান সমস্যা। আবার কেউ মনে করেন প্রকৃত সমস্যা নিহিত ইতিহাস, শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনীতি, সামাজিক বৈষম্য আর ঔপনিবেশিক শোষণে।
কিন্তু কারণ যাই হোক, আজকের বাস্তবতা সবাইকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আশু বিপর্যয়ের আভাস। কতকগুলো গুরুতর পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যার দ্রুত সমাধান না ঘটলে সারা দুনিয়ার সামনে সমূহ বিপদ ঘনিয়ে আসবে। বিশাল গ্রীষ্মমণ্ডল জুড়ে বনভূমি নিশ্চিহ্ন হচ্ছে, ভূমির উর্বরতা কমছে, নানা অঞ্চলে মরুসদৃশ অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে, কীটপতঙ্গের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক দেশে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে।
তেমনি বাড়ছে সামাজিক বৈষম্য; প্রাকৃতিক সম্পদের নির্বিচার ব্যবহার পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করছে। এসব সমস্যার সমাধানে জীববিজ্ঞানের যেমন ভূমিকা রয়েছে তেমনি রয়েছে সমাজবিজ্ঞানেরও।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জীববিদ্যার প্রয়োগ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাপক অবদান রেখেছে। রোগ-ব্যাধি নিরাময়ে নাটকীয় অগ্রগতি ঘটেছে, বংশগতিবিদ্যার প্রয়োগে এবং নানা জৈব পদ্ধতিতে প্রভাব বিস্তারের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এবার এই জ্ঞানকে পৃথিবীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অধিবাসী অধ্যুষিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের সমস্যার ক্ষেত্রে আরো আরো সার্থকভাবে প্রয়োগ করার জন্য জীববিজ্ঞানীরা সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করছেন। সেই সাথে তাঁরা হাত মেলাচ্ছেন অর্থনীতিবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের বিজ্ঞানীদের সাথে।